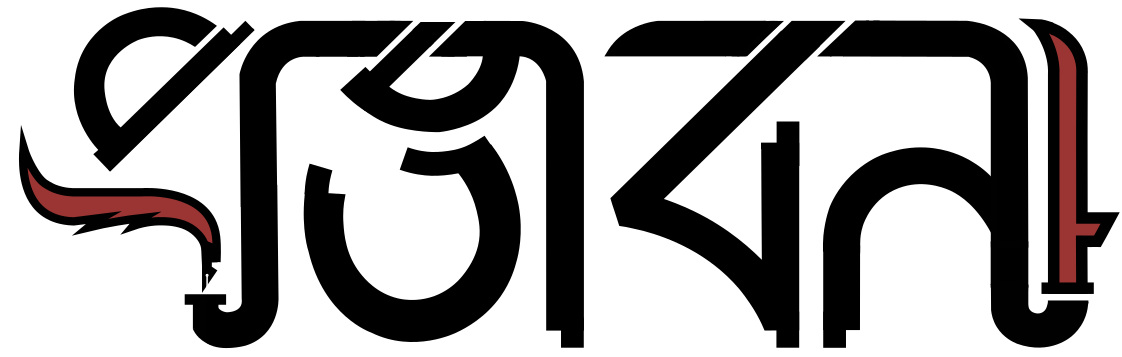অধ্যাপক সালমান সায়্যিদের আলোচিত ‘রিকলিং দ্য কেলিফেইট' বইয়ের ‘সেকুলারিজম' অধ্যায়ের অংশবিশেষ নিম্নে বাংলায় পেশ করা হলো।
সেকুলারিস্টরা গন পরিসরে খোদা, ফেরেশতা বা শয়তান নিয়ে কোন আলাপ দেখতে চায়না, কারণ তারা মনে করে হালের ভয়ানক খুনাখুনির পেছনে ‘সেকুলার’ আর ‘রিলিজিয়াস’ এ দুয়ের মাঝে সঠিকভাবে পার্থক্য না করতে পারার জন্যই এসব ঘটছে। আকীল বিলগ্রামী বলেন,
“যতো সময় পেরোচ্ছে ততোই নিজেকে সেকুলারিস্ট হিসেবে ঘোষনা দেয়ার জরুরত অনুভব করছি (এবং এখানে আমাকে তা-ই বলে ঘোষনা দিচ্ছি)। বিশেষ করে এই সময়ে যখন ডানপন্থী খৃষ্টবাদ দ্বারা প্রভাবিত সরকার যুদ্ধ বাজিয়ে যাচ্ছে, ইসলামের নামে ‘টেরর’ ছড়ানো হচ্ছে, সুস্পষ্ট ইহুদী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে বাস্তুচ্যুত জনপদের ভুখন্ডগুলোতে দখলদারিত্ব চালাচ্ছে এবং কল্পিত হিন্দু গরীমা পূনর্জাগরনে একটি সংখ্যাগরীষ্ঠ গোষ্ঠী পরিকল্পিত দাঙ্গা বাধিয়ে আরেক অবরুদ্ধ সংখ্যালঘু জনপদকে হত্যা করছে” (২০০৪:১৭৪)
এর বিপরীতে সাবা মাহমুদ প্রয়োজনীয় কিছু যুক্তি পেশ করেন,
“সেকুলারিজম পোক্ত করার জন্য নতুন করে এর প্রতি পবিত্র ও কড়া দাওয়াত পেশের পরিবর্তে জরুরী হলো এর ব্যাপারে চালু থাকা পরম সত্য, মাননির্ধারক দাবী, এবং এই বিশ্বে মানুষের সংজ্ঞা নিয়ে এর ধারণাগুলো ক্রিটিকাল বিশ্লেষণ করা। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে চিত্তাকর্ষক বলে এই কাজ করবো তা নয়, বরং সেকুলার ভিশনের নৈতিক শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আমরা যা ভাবি সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে পূনর্চিন্তা করার প্রয়োজন এসে পড়েছে।” (২০০৬:৩৪৭)
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে আকিদা সংস্কারের প্রচারাভিযান চলে তার সাথে “মডারেট মুসলিম” শীর্ষক কিছু চিন্তকের লেখার মিল নিয়ে সাবা মাহমুদ বেশ বিশ্লেষণ করেছেন যেখানে তারা ইসলামের এক ধরণের সেকুলারিস্ট ব্যাখ্যা হাজির করেন। বিলগ্রামি হয়তো এই মিলকে কাঁকতলিয় বলবেন। তিনি সেকুলারিজমের বিভিন্ন শত্রুদেরকে (ডানপন্থী খৃষ্টান, ইসলামিস্ট, হিন্দুত্ববাদী ও চরম্পন্থী জায়োনিস্ট) এক কাতারে ফেলে এমন এক তাত্ত্বিক সমন্বয়বাদ তৈরি করেন যেখানে এই আপত্তি তোলা সম্ভব হবে না যে, সেকুলারিজম মুসলিম মারার আরেকটা লাঠি বৈ কিছু নয়। বৈশ্বিক এন্টি-সেকুলারিস্ট শক্তিগুলো একসাথে মিলে কাজ করছে এ দাবী করার জন্য বেশ কতগুলো অসমঞ্জস্য চাপাবাজির দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ যদি ফিলিস্তিনবাসীদের উপর দখলদারিত্ব ও অত্যাচার চালানো ইসরাইলের মাঝে ধর্মীয় বৈধতা খুজতে চায় তাহলে জায়োনিস্ট রাষ্ট্রের মূল ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী (judaic terms) সেটা প্রমান করতে হবে ইহুদী জনপদ-ভিত্তিক যুক্তির (jewish terms) বাইরে বেড়িয়ে [ইহুদীদের ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী বিশুদ্ধ ধর্মভিত্তিক যুক্তির (judaic terms) মাধ্যমে ইসরাইলী জায়োনিস্ট রাষ্ট্রের বিরোধীতা করে থাকে কারণ মসীহ আসার আগে ইসরাইলী কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তারা অস্বীকার করেন।] নাকি আমরা বলবো ভারতের পরিকল্পিত দাঙ্গাগুলো শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদী সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়ামাত্র এবং তা নেহরুভীয় সেকুলার হেজেমনির সবচেয়ে শক্তিশালী সময়ে ছিলনা? এটা কি সত্য না যে বড় আকারের নৃশংসতাগুলো (যুদ্ধ, ‘সন্ত্রাস’, দখলদারিত্ব, দাঙ্গা) ধর্ম ব্যাতীত কল্পনা করা যায়না? আমরা কি আরেকটা তালিকা করতে পারবোনা যেখানে মহাযজ্ঞ ও হিংস্রতার প্রদর্শনীর মহানায়করা সবাই সেকুলার ছিলেন?
বিলগ্রামির উল্লেখিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ, ইসলামের নামে সন্ত্রাস, জায়োনিস্ট দখলদারীত্ব এবং ভারতের সঙ্ঘবদ্ধ নির্যাতনের কেইসগুলোতে আরেকটি সাধারণ সূত্র পাওয়া যায় আর তা হলো ইসলাম ও মুসলিম -- এ দুটো বিষয় প্রতিটি কেইসে পাওয়া যাবে। মুসলিম সক্রিয়তা এবং বর্তমান বিশ্ব ব্যাবস্থার মধ্যকার সম্পর্ককে সেকুলারিজমের সমস্যা এবং এর অস্বস্তি হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এই লেখাতে সেকুলারিজম কীভাবে মুসলিম সক্রিয়তার সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে সেটা তুলে ধরা হবে যেখানে সেকুলারিজম সর্বদা মুসলিম সমস্যার সমাধানমূলক আলোচনায় কাঁকতলিয়ভাবে নিজেকে দেখতে পায়।
সেকুলারিজম তার সবচেয়ে সরল এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত অবয়বেও ধর্ম (ইংরেজি religion এর শাব্দিক অর্থ হিসেবে) ও রাজনীতির কার্যত পৃথকীকরণ চায়, বিধিগতভাবে না হলেও। গোট বিশ্বের জন পরিসরে পুনরায় ইসলামকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্পকে প্রগতিবাদী বৈশ্বিক সেকুলারায়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন হুমকির মধ্যে গণ্য করা হয়। এটা ঠিক যে, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে (অন্তত) চার্চ ও স্টেট আলাদাকরনের আলাপগুলো ডানপন্থী নাসরানীদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নড়চড়া দ্বারা মৌলিকভাবে প্রভাবিত। তবে,নির্দোষভাবে তাকালে দেখা যাবে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ বৈশ্বিক রাজনৈতিক শাসন পদ্ধতির ব্যাকরন হিসেবে আবির্ভূত হবার ফলে বৈশ্বিক সমস্যা আকারে সেকুলারিজম সংক্রান্ত আলোচনাগুলো ইসলামিকেট উদাহরণ ও ঘটনা দ্বারা পরিবর্তিত হয়। পশ্চিম ধনিকতন্ত্রবাদী মহলের (plutocracies)সাম্প্রতিক আলোচনাগুলো মুসলিম সংখ্যালঘুদের সেকুলার হওয়া দরকার শিরোনামে মনোযোগ ধরে রেখেছে। নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন সম্পন্ন এবং বেশিরভাগ সময়েই প্রাক্তন উপনিবেশকৃত অঞ্চল থেকে আসা জনপদকে কিভাবে সমাজের অংশ করা যায় এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো সেকুলারিজম প্রকল্পের ইস্যুগুলোর মোড়ক হিসেবে হালের ওয়েস্টফেলিয় বিশ্ব কাঠামো এবং সেকুলারিজমের মতো জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যকার ডিস্কার্সিভ মিলগুলো পুনরায় শক্তিশালী এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনরায় হাজির করেছে। মুসলিম সংখ্যালঘু ‘সমস্যাটি’ জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তি এবং নৃতাত্ত্বিকভাবে চিহ্নিত শক্তির মধ্যকার সম্পর্কের কলকব্জা সংক্রান্ত জন-নীতিমালার প্রশ্ন শুধু উঠিয়ে আনেনা, বরং পশ্চিম এন্টারপ্রাইজ যে ‘বিশ্বজনীন ভাষার’ প্রস্তাব রাখে এবং সেই ভাষা এন্টারপ্রাইজের বেহাতকরন প্রতিরোধ করার পাশাপাশি মুসলিমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত কিনা – এ সংক্রান্ত আদর্শিক প্রশ্নগুলোও তুলে আনে।
সেকুলারিজমকে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক গঠনের অন্যতম একটি অর্জন বলে পেশ করা হয়। এর অনুমিত উপকারগুলোকে তিনটি প্রশস্ত গুচ্ছে ভাগ করা যায়। জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তিগুলোর একটি গুচ্ছ দাবী করে যে সেকুলারিজম ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব নয় যা অবশ্যই আবার প্রযুক্তির অগ্রগতিকে পোক্ত করে। এই দিক থেকে সেকুলারিজম সামাজিক বিভাগের বদলে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিভাগ হিসেবে আসবে যেখানে জ্ঞানকান্ডের কেন্দ্র খোদা হতে মানবে স্থানান্তরিত হয়েছে। এর প্রধান যুক্তি হচ্ছে যে সেকুলারিজম ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের দাবীগুলোকে অন্যায়সঙ্গত করে যাতে জ্ঞানের উৎপাদন নিয়ন্ত্রন করা যায়, এবং এমন পরিস্থিতির তৈরি করে যেখানে ধর্মীয়/পবিত্র বর্ণনায় প্রাপ্ত অন্টোলজিকাল দাবীগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে একটি বিজ্ঞানকেন্দ্রিক অন্টোলজি পছন্দ করা হয়।
দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তিগুচ্ছে সেকুলারিজমের নাগরিক কল্যানের দিকগুলোর উপর জোর দেয়া হয়। এই গুচ্ছের দাবী মতে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় এবং ধর্মীয় অনুভূতির তীব্রতা নিয়ন্ত্রনে রাখতে সেকুলারিজম জরুরী। ধর্মকে আলাদা করে ব্যাক্তিগত জায়গায় সীমাবদ্ধ রেখে সেকুলারিজম আন্তঃধর্মীয় বিবাদগুলোকে গনপরিসরে কোন ধরণের সংঘাতের কারণ হিসেবে দায়ী থাকা হতে বিরত রাখে। আন্তঃধর্মীয় দ্বিমতগুলো ব্যাক্তিগত রুচিতে পর্যবসিত হয়, সুতরাং এটি সামাজিক জীবনে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পারেনা। এছাড়াও বিভিন্ন বিবাদমান দল যাতে আধিদৈবিক শক্তির দোহাই দিয়ে তাদের অবস্থানগুলো শক্ত করার প্রয়াস না চালাতে পারে, এবং সবাই যে একটি সমতাপূর্ণ প্রযোগীতামূলক ক্ষেত্রে তর্ক করবে সেটি যাতে উক্ত দোহাইয়ের কবলে ধ্বসে না যায় – সেকুলারিজম এটি নিশ্চিত করে।
তৃতীয় প্রকারের গুচ্ছে বলা হয়ে থাকে যে, সেকুলারিজম গনতন্ত্রচর্চার জন্য একটি জরুরী পূর্বশর্ত: এটি খোদা অথবা যারা খোদায়ী সিলসিলার দাবী করে তাদের দ্বারা কোন ধরণের ক্ষমতা গ্রহণ প্রতিরোধ করে যা ক্ষমতার জায়গাকে কার্যত শূন্য করে রাখতে সাহায্য করে। খোদাকে অপসারণের মাধ্যমে ক্ষমতার জায়গা খালি করার সুযোগ তৈরী হয়। দাবী হচ্ছে যে, গনতন্ত্র ‘জনগণের সার্বভৌমত্বের’ ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে (এখন এই ধারণাটি বাস্তবে কতোটুকু পালিত হয় সেটি ভিন্ন আলাপ; যেমন: ব্রিটেনে সংসদ হচ্ছে সার্বভৌম, জনগন নয়, যদিও সংসদের ক্ষমতা জনগণ হতে প্রতিপাদিত হয়)। জনভিত্তিক সার্বভৌমত্ব কোন প্রকারের সার্বভৌম খোদা বা সার্বভৌম পৌরহিত্যের ধারণাকে অসম্ভব করে তোলে।
সুতরাং সেকুলারিজমের উপকারগুলো স্বয়ং আধুনিকতার ধারণাকেই গড়ে তুলতে সাহায্য করে (অবশ্য এটি প্রযোজ্য শুধু জনপ্রিয় সংস্করনের আধুনিকতার ব্যাপারে যার সাথে পশ্চিম পরিচয়ের সম্পর্ক রয়েছে। মার্টিন জ্যাক (২০১২) আলাদা করে পূর্ব-এশিয় আধুনিকতা নিয়েও আলাপ করেছেন)। আধুনিকতা অবশ্যই পশ্চিম পরিচয়ের ব্যাতিক্রমতার উপাখ্যানকে নির্দেশ করে এখনো; সুতরাং সেকুলারিজম নিজেই পশ্চিম পরিচয়ের একটি চিহ্নায়ক হিসেবে হাজির হয়। অতএব, পশ্চিম নৃচিত্রের মাঝে একটি মুসলিম কর্তাসত্তার অবস্থানকে গ্রন্থিবদ্ধ করা পশ্চিম পরিচয়ের জন্য বেশ অদ্ভুত/সমস্যাকর হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিমরা শুধুমাত্র ‘মুসলিম’ হওয়ার গুণেই প্রতি-সেকুলারিজমের বাহক বনে যায় কারণ এই এই পরিচয়ের ব্যাখ্যা ধর্মীয় বাদে কিছু হতে পারেনা, তাই পশ্চিম ধনিকগোষ্ঠীর ভূগোলগুলোর জনসমক্ষে মুসলিমদের দৃশ্যমান উপস্থিতি সেকুলারিজম যে ধর্ম-রাষ্ট্র বিভাজন করতে চায় তাকে মুছে দিতে চায়। এলাকোত্তীর্ণ মুসলিম সত্তার পুনঃসক্রিয়তা পশ্চিমের সাপেক্ষে ইসলামের পাল্টা-বাস্তবতামূলক প্রকৃতিকে সামনে নিয়ে আসে। সুতরাং ইসলামের সেকুলারিজমহীনতা পশ্চিমের সেকুলারিজমের সাথে তুলনা করা হয় যার সাহায্যে (কোন) সভ্যতার অগ্রসরতার জন্য সেকুলারিজমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করা হয়। ইসলাম এখানে শুধুই পাল্টা-ইতিহাস হিসেবে আসেনা; এটি মুসলিমদের মাঝে একটি নিজস্ব-স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গঠনের চিহ্নায়ক হিসেবে জারী থাকে; ফলে, সেকুলারিজমকে একটি বিশ্বজনীন গুরুত্বের জায়গা থেকে উপকারী দেখানোর প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। অন্য কথায়, পশ্চিম থেকে ইসলামিকেইট সমাজে সরে আসলে সেকুলারিজমের বিশ্বজনীন দাবীগুলো দুর্বল হতে দেখা যায়।
এটা ক্রমশই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে সকল সামাজিক গুচ্ছের মধ্যে মুসলিমরাই সেকুলারিজমের দাবীগুলো না গ্রহণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রখ্যাত (এর অর্থ এই নয় যে, এমন কোন মুসলিম নেই যে সেকুলারিজমের দাবীগুলো প্রত্যাখ্যান করেনা। বরং নোংরা বৈশ্বিক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পশ্চিম ধনিকতন্ত্রের ভূগোলে অনেক সংস্থা উঠে এসেছে যারা সেকুলার বা মডারেট ইসলাম প্রচার করে, যেমন: প্রোগ্রেসিভ মুসলিমস, মুসলিমস ফর সেকুলার ডিমোক্রেসি। তা সত্ত্বেও এটা সত্য যে এর চেয়েও বেশি মুসলিম মুসলিমত্বকে শাসন করার হাতিয়ার হওয়ার জন্য সেকুলারিজমকে সমালোচনা করে থাকে।)। এর আংশিক কারণ হচ্ছে পশ্চিম ইতিহাস আর ইসলামিকেইট ইতিহাস সেকুলারিজমের জরুরত বা অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে কী বলতে চায় তাতে পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে, মুসলিমদের জন্য সেকুলারিজমের প্রধান তিনটি যুক্তির প্রায়োগিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতাকে স্বাধীন ইসলামিকেইট সাংস্কৃতিক গঠনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চ্যালেঞ্জ করা করা যায় যেগুলো এই গ্রহের উপনিবেশায়িত কাঠামোর আগে অস্তিত্বশীল ছিল।
সেকুলারিজমের পক্ষের দাবীগুলোর সমস্যা হচ্ছে যে এগুলো প্রায়শই ওয়েস্টার্নিজের1 বয়ানের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়, এবং এভাবে পশ্চিমের ঐতিহাসিক গঠনকে বিশ্বজনীন প্রাসঙ্গিকতার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। […]পশ্চিম ইতিহাসের প্রসঙ্গ কাঠামো ধরে আগালে দেখা যাবে, পশ্চিম সেকুলারিজম পশ্চিমের কোন নিজস্ব ইতিহাস নয় যেখানে এটি একটি নির্ভরশীল ঘটনাচক্র হিসেবে বিদ্যমান, বরং এটি বিশ্বজনীন ইতিহাসের অংশ হিসেবে জরুরীভাবে আবির্ভুত হয়েছে। সেকুলারিজম তখন হয়ে যায় একটি আবশ্যিক মঞ্চ যেখানে না দাঁড়িয়ে কোন সাংস্কৃতিক গঠন আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হতে পারবেনা।
সুতরাং, উদাহরনস্বরূপ, সেকুলারিজমের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞান ও চার্চের দ্বন্দের মাঝে – যেই সংঘাত প্রতিকায়িত হয়েছে গালিলেওর বিচারের মধ্য দিয়ে। কোন সঙ্ঘবদ্ধ চার্চাব্যাবস্থা না থাকায় ইসলামিকেইট সমাজে বিজ্ঞান ও ধার্মিক কর্তৃত্বের মাঝে এমন পরিষ্কার দ্বন্দ্ব/সীমানা নির্ধারন করা কঠিন। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে, খোদায়ি বিষয় বোঝার জন্য ইসলাম ও নাসরানি বয়ান তুল্যরূপ – এই ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেকুলারিজমের উপকারীতার জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি।
খোদায়ীতার উপর খৃষ্টতাত্ত্বিক ও ইসলামি বয়ানগুলো জরুরী বা মৌলিক হিসেবে দেখা যাবেনা, কেননা খোদায়ীতার উপর চিন্তাভবানার পার্থক্যগুলো বৈচিত্রময় ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক ধারাগুলোর অন্তর্গত আলাপগুলো তুলে ধরে, খৃষ্টবাদ কিংবা ইসলামের মধ্যে যে বিশেষ নিজস্ব মৌলিকতা খোদাই করা আছে সেগুলো না। যেটা করলে উপকার হবে তা হলো: খোদায়ীতার প্রকৃতির উপর বিভিন্ন অবস্থানগুলো তুলে ধরা – যেগুলো আলাপটির জটিলতা এবং এর উপর একাধিক মতামতের উপর ভিত্তি করে দাঁড়ানো পোক্ত বৈশিষ্ট্যযুকরণ প্রক্রিয়ার আলোকে বের করা হবে। প্রাথমিক নাসরানি উপদলীয় কোন্দলগুলোর অনেকগুলোরই খৃষ্টতাত্ত্বিক মাত্রা ছিল, যেমন, যারা কাউন্সিল অব ক্যালসিডেন এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করতো এবং যারা করতোনা তাদের মধ্যকার বিতর্কগুলো – আরিয়ানরা, নেস্টোরিয়ানরা, আর মনোফিসাইটরা। ক্যালসিডেনিয় ব্যাখ্যার আধিপত্য খোদায়িতার এমন এক খৃষ্টতাত্ত্বিক ধারণার উৎপত্তি করে যেখানে খোদায়ীতা এবং জাগতিকতার সত্তাতাত্ত্বিক ভিত্তি একই। দেহধারন বা অবতারতত্ত্বের আলোকে মানব জগত এবং খোদায়ী বাস্তবতার যে সংযুক্তির ফলে খৃষ্টের দেহে জাগতিকতা ও খোদায়িতা সম্মেলন হয়, সেটি নিঃসন্দেহে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দাড় করিয়ে রাখে যেখানে মানুষের চেষ্টা প্রচেষ্টা সম্ভপরতায় খোদায়ীতার সাথে প্রতিযোগীতা করতে পারে। খোদায়ী কার্যকরন এবং হস্তক্ষেপের এই আখ্যানগুলো মানব সক্ষমতার আখ্যানের সাথে একটি জিরো-সাম গেইমে আটকে যায়। ফলত বিজ্ঞান ও ধর্ম বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।
ইসলামি ব্যাখ্যাগুলোতে খোদায়িতা ও মনুষ্যতার মধ্যকার পার্থক্যগুলো মেটানো সম্ভব না। খোদায়ীতার উপর ইসলামিকেইট চিন্তাভাবনাগুলো মানুষ ও খোদায়ী জায়গাগুলোর মধ্যকার ব্যাবধান বজায় রাখতে নিয়মিতভাবে সক্ষম হয়েছে – এই ব্যাবধান প্রশস্ত এবং চিরস্থায়ী। সুতরাং কোন মানুষ খোদায়ীতার কেন্দ্রিকতাকে অবলম্বন কিংবা প্রতিস্থাপন করতে পারবেনা, যেখানে মানুষ ও খোদা তাদের নিজস্ব সত্তাতাত্ত্বিক বাস্তবতায় অবস্থান করে যেটা মিলানো সম্ভব না। সুতরাং, বিজ্ঞান আকল বা বুদ্ধি-যুক্তির উপশাখা হিসেবেই থাকবে এবং একিসাথে খোদার ভুমিকা বা কর্তৃত্বকে অস্বীকার করবেনা।
নাগরিক শান্তি বজায় রাখার জন্য সেকুলারিজমকে জরুরী হিসেবে দেখানোটি দাঁড়িয়ে আছে রেফর্মেশন এবং কাউন্টার-রেফর্মেশন যুদ্ধের ইউরোপিয়ান অভিজ্ঞতারলব্ধ বা উৎসরিত আখ্যান থেকে যার মাধ্যমে নাগরিক শান্তি বজায় ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বি-রাজনীতিকরণের মধ্যকার সম্পর্ক সাধারণভাবে তুলে ধরা হয়। আগেই দেখানো হয়েছে যে, এমন মাপের ও তীব্রতার উপদলীয় মারামারির উদাহরণ ইসলামিকেইট ইতিহাসে নেই, সুতরাং নাগরিক শান্তি বজায়ের জন্য ধর্মকে ব্যাক্তি পর্যায়ে সীমিত রাখতে হব এই ধারণাটি সরলভাবে ইসলামিকেইট ইতিহাস থেকে পড়া যাবেনা। সন্দেহ নেই বড় মাপের রুক্ষতায় কিছু উপদলীয় কোন্দল হয়েছে, যেমন, প্রথম ও দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ (৩৫- ৪০ হিজরি/৬৫৬-৬৬১ খৃষ্টাব্দ এবং ৬০-৭৩ হিজরি/৬৮০-৬৯২ খৃষ্টাব্দ) – কিন্তু এই বিবাদ্গুলো প্রধানত উচ্চপর্যায়ের ক্ষমতাধরধের মধ্যে ছিল এবং এগুলো জনগণের কোন প্রকার বড়সড় অংশগ্রহণ বা গনহত্যার দিকে নিয়ে যায়নি। ফাতেমী ও আব্বাসীদের মধ্যকার বিবাদ (২৯৬-৫৬৬ হিজরি/৯০৯-১১৭১ খৃষ্টাব্দ) সম্ভবত খৃষ্টীয় দুনিয়া তছনছ করে দেয়া ধর্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যবাহী বিরোধিতার কাছাকাছি যেতে পারে, কিন্তু আব্বাসী ও ফাতেমী রাজনৈতিক ক্ষমতাগোত্রের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অবস্থা ইউরোপের ধর্ম যুদ্ধে যে ধরণের তীব্র সহিংসতার অভিজ্ঞতা হয়েছে সেরকম কিছু উৎপন্ন করার জন্য যথেষ্ট ছিল না।
বরঞ্চ এর বিপরীতটাই ভাস্বর হয়ে উঠে, যেখানে, ইসলামিকেইট ইতিহাসে, জনপরিসর থেকে ধর্মের অনুপস্থিতিই নাগরিক অস্থিতিশীলতার সাথে জড়িত। তুরস্কের খুব সমাদৃত সেকুলার গঠন, উদাহরনস্বরূপ, চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল একটি ক্লান্ত এবং যুদ্ধশ্রান্ত জনগণের উপর। তুর্কি গনপ্রজাতন্ত্রের সেকুলারিজম তুর্কি জনপরিসরের কোন দাবীর মোতাবেক ছিলনা, বরং এটি এসেছে কামালবাদীদের পশ্চিমায়নের কর্তৃত্ববাদী প্রকল্প হতে। ইসলামিকেইট সমাজের প্রেক্ষাপটে সেকুলারিজম প্রায়শই বি-ইসলামীকরণ বুঝিয়েছে, এবং অধিকাংশ সময়েই উপনিবেশী, কমিউনিস্ট, কিংবা কামালবাদী প্রশাসন কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলোর সবগুলো সমাজের বিবাদগুলো বাড়িয়েছে বৈ কমায় নি। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মুসলিম দেশগুলো বিঘোষিত সেকুলার প্রশাসন দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার পাল্লা ও তীব্রতা এমন ছিল যে সেকুলারিজম এবং নাগরিক শান্তির মাঝে কোন যোগাযোগ স্থাপন করার অনুপ্রেরণা এখান থেকে পাওয়া যায়না।
গণসার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক ব্যাবস্থার জন্য সেকুলারিজম একটি পূর্বশর্ত – এই দাবিটি গণসার্বভৌমত্বের বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যাগুলোকে উপেক্ষা করে: বিভিন্ন ধরণের সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে শুরু করে মওদুদি এবং অন্যান্যদের ব্যাখ্যাগুলো যেখানে তাঁরা গণআকাঙ্ক্ষাকে সার্বভৌমের বদলে সার্বভৌম-প্রতিনিধি (Vice-Regal) পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, খোদায়ি সার্বভৌমত্ব সারা জাহানে খোদার কেন্দ্রিকতার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যার অংশ হলেও এটি একটি বাস্তবিক সার্বভৌমত্ব হতে পারবেনা এই অর্থে যে ‘সার্বভৌম হচ্ছে তিনি যিনি ব্যাতিক্রমের উপর সিদ্ধান্ত নেন’ (শ্মীট, ২০০৫:৫), শুধু এ কারনেই যে সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ খোদার একত্ববাদী ব্যাখ্যা খোদায়ীতার ব্যাপারে কোন ব্যাতিক্রম থাকার অবকাশ দেয় না (অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে একটি বিশেষ খোদায়ী সিদ্ধান্ত সত্যিকারভাবে চেনার তকলিফ বিদ্যমান থাকা)।
দেখা যাচ্ছে যে সেকুলারিজমের অর্থ ‘প্লেটো থেকে ন্যাটো’ অনুক্রমে ঢুকে গিয়েছে যা ওয়েস্টার্নিজকে সজ্ঞায়িত করে। কারণ একটি বৈশ্বিক মুসলিম কর্তাসত্তার ধারণা ইউরোপের ‘চূড়ান্ত শব্দমালার’ স্থানীকরণ করে – এটি প্ল্যাটো থেকে ন্যাটোকে ইতিহাসের বদলে একটি ইতিহাসতাত্ত্বিক অনুমান হিসেবে উন্মোচিত করার হুমকি দেয়। পশ্চিম ধনিকতন্ত্রে বসবাসরত মুসলিমদের উপস্থিতি এর ‘অভিবাসি’ কল্পনায় সমস্যা তৈরি করে যেখানে ধর্ম, সংখ্যালঘু, ‘রেইস’ ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগগুলো বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষনের ফল হওয়ার বিপরীতে প্ল্যাটো থেকে ন্যাটো অনুক্রমের অংশ হিসেবে উঠে আসছে। এটা প্রমান করে যে এই অনুক্রমের বৈধতা উপনিবেশিতা চর্চার উপর দাঁড়িয়ে আছে। উপনিবেশিতাকে উপনিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বোঝা যাবেনা, বরং এটি হচ্ছে সরকারীতার একটি যুক্তিগোত্র যা ঐতিহাসিক উপনিবেশের বিশেষ কিছু রূপের উপর দাঁড়িয়ে উপনিবেশের আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিকরন ছাড়িয়ে একটি গ্রহব্যাপী ক্রমাধিকারতন্ত্র গঠন করে যায় পশ্চিম আর অ-পশ্চিম বিভাজনের ভিত্তিতে (এবং এর থেকে উদ্ভূত যা আছে)।
সেকুলারিজমের পক্ষে নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক যুক্তিগুলো খণ্ডন করা হচ্ছে এর প্রায়োগিকতাকে আরো প্রশস্ত করার চেষ্টা করা। দুইভাবে এই প্রশস্তকরণ হয়: ঐহাসিকভাবে, ভৌগলিকভাবে। ঐতিহাসিকভাবে সেকুলারিজমে প্রশস্ত করা হয় এভাবে যে এটি ওয়েস্টফ্যালীয় আবিস্কার নয় এবং ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধির (১০৫৮/১৬৪৮) আগেও সেকুলারিজম ছিল। এর ফল হলো জাতিরাষ্ট্র-পূর্ব দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক কাঠামো বা সাম্রাজ্যগুলোকে সেকুলার হিসেবে দেখানো; যেমন, এটা বলা যে, মুসলিমিস্তানেরও একটি নিজস্ব সেকুলারিজম রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি করা হিসেবে আনা হয় কিছু হাদিস যেখানে রাসুল সা. সিদ্ধান্ত ও কর্মের মাঝে তফাৎ টেনেছেন খোদায়ী অহী এবং মনুষ্য জ্ঞান ও যুক্তির জায়গা থেকে। এই পার্থক্যকরণ নবী-পরবর্তী যুগে সমস্যার তৈরি করে কারণ এর অর্থ দাঁড়াবে যে, হযরত জিবরাইল আ. সরাসরি আপনাকে না বলা ব্যাতিত কোন কিছু ধর্মিয়/অ-সেকুলার হতে পারেনা। অতএব সেকুলার আর ধর্মীয় এ দুটোর মধ্যকার বিভাজন ধ্বসে যাবে কারণ এখানে সেকুলার ধর্মীয়কে সম্পূর্ণভাবে করতলগত করে বা উপনিবেশায়িত করে। এই অবস্থানটি শুধুমাত্র একটি চাক্রিক যুক্তির ফাঁদে দিয়ে রক্ষা করা সম্ভব যেখানে সেকুলারিজমের আধিপত্যই শুধুমাত্র সেকুলার আর ধর্মীয় এর মধ্যকার বিভাজন সংজ্ঞায়িত করবে। ধর্ম এভাবে সেকুলারিজম দ্বারা তৈরি একটি উপ-বিভাগ হিসেবে আবির্ভুত হয়। অবশ্যই সেকুলারিজমের নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে পশ্চিম আলোকায়নের মাঝে, সুতরাং একে এই সময়ের বাইরে নিয়ে ব্যাপ্তি বাড়ানোর অর্থ হচ্ছে এই বিশেষ পশ্চিমীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে পুরো বিশ্বের ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করা। অ-ইউরোপীয়দের মধ্য থেকে সেকুলারিজমের পূর্ববর্তী উদাহরণ খোঁজার বদলে অন্য সমাজগুলোর ইতিহাসতত্ত্বে সেকুলার/ধর্মীয় বিভাজন আরোপ করা ওয়েস্টার্নিজের প্রভুত্বকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।
যে পন্থায় সেকুলারিজমের ধারণা ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে ছিড়ে অ-ইউরোপীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এবং (কোন আশ্চর্য ছাড়াই) গুরুতর অসংগতির উৎপন্ন করে সেটি সন্তোষজনক কিছু নয়। এই পন্থাটি মূলত সেকুলারিজম যে মৌলিকভাবে ইউরোপীয় সেই ধারণাকেই পোক্ত করে যদিও তা অস্বীকার করতে চাওয়া হয়।
ভৌগলিকভাবে সেকুলারিজমকে নিয়ে যাওয়া হয় অ-পশ্চিম জায়গাগুলোতে যাতে দেখানো যায় সেকুলারিজম শুধু পশ্চিমে পাওয়া যায়না, এর বাইরেও তার অস্তিত্ব আছে। ভারতীয় সেকুলারিজম এরকম একটি উদাহরনের ক্ষেত্র তৈরি করে। ভারতীয় (উদারনৈতিক-মহাজনরা) ভারতের গণ পরিসরে সেকুলারিজমের ভুমিকা নিয়ে ব্যাপক নড়াচড়া করেছেন। বলা হয়, ভারতীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘ আয়ু, এর আপেক্ষিক নাগরিক শান্তি (কাশ্মির, নাগাল্যান্ড আর পাঞ্জাবের কতিপয় ‘বিদ্রোহ’ বাদে অবশ্যই) এবং ‘ইন্ডিয়া শাইনিং’ এর দিনগুলো থেকে এর বাড়ন্ত অর্থনীতি – এ সবগুলোই কীভাবে পশ্চিম ইউরোপ বাদে ভারতের মতো একটি এলাকায়ও সেকুলারজিম উপকার বয়ে আনে তার দিকে ইঙ্গিত করে। ভারতের সমৃদ্ধি, গণতন্ত্র, এবং নাগরিক শান্তি বজায় এগুলো সেকুলারিজমের প্রতি ভারতের শাসক মহলের অঙ্গীকারবদ্ধতাই নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। যদি ভারতে এই সেকুলারিজম কাজ করে, তাহলে হয়তো এর বিশ্বজনীন দাবীগুলো আবার পুনরুদ্ধার-পুনস্থাপন করা সম্ভব হবে। যদিও আমরা বলতে পারি যে ভারতীয় সেকুলারিজমের মূলে রয়েছে পশ্চিম: আধুনিক ভারত ব্রিটিশ রাজের উত্তরসূরি হিসেবে অসংখ্য উপনিবেশী সরকারিতা অবলম্বন করেছে যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্বতন্ত্র ধর্মীয় গোত্রের ব্যাপারে গৃহিত সংজ্ঞা ও আইন-কানুন। ভারতীয় সেকুলারিজমের প্রধান তাত্ত্বিক নেহরু ভারতকে চিনত ‘ইন্ডোলজি/ভারতবিদ্যার’ মধ্য দিয়ে (ব্রাউন, ২০০০)। ভারতীয় সেকুলারিজমের জটিল জন্মসূত্রীতা পশ্চিম সেকুলারিজমের চেয়ে ভিন্ন কোন স্বতঃস্ফুর্ত ভারতীয় সংস্করণ আনতে পারেনা যা দীর্ঘ আলাপে দণ্ডায়মান থাকবে। ভারতে সেকুলারিজম তিনভাবে আনা হয়।
প্রথমত, ভারতকে পাকিস্তান থেকে ভিন্ন করার জন্য সেকুলারিজম আনা হয়। ১৯৪৭-এর ঘটনার পরে ব্রিটিশ রাজের উত্তরসূরী হিসেবে দক্ষিণ এশিয়াকে প্রায়শই উপস্থাপন করা হয় একটি আত্মস্বীকৃত রাষ্ট্র এবং আরেকটি সেকুলার রাষ্ট্রের তুলনামূলক পাঠ হিসেবে। এই ভারত-পাকিস্তান তুলনা, যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসতত্ত্বের অধিকাংশ এলাকা দখল করে থাকে, সেকুলারিজম এবং তার বিশ্বজনীন বঈধতার জন্য যুক্তি হিসেবে কাজ করে। ভারতীয় সেকুলারজিম পাকিস্তানের সাপেক্ষে ভারতের চরিত্র নির্ধারণ করে (বিশেষ করে নেহরুভীয় বয়ানে যেটি দেশভাগের পর অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে আধিপত্যশীল ছিল) যেখানে ভারত হচ্ছে গণতান্ত্রিক এবং স্বাভাবিক রাষ্ট্র এবং পাকিস্তান হচ্ছে একটি ইসলামী ও ব্যার্থ রাষ্ট্র। এই তুলনামূলক পাঠ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যকার এক প্রকার সাদৃশ্যতা উপেক্ষা করে, যেমনটা আয়েশা জালাল বলেন, যে, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র’ এই ফাঁকা বুলি এবং পাকিস্তানের দীর্ঘ সামরিক নির্ভরশীলতার (Praetorianism) পেছনে এক জটিল কর্তৃত্ববাদ কাজ করে যা স্বচ্ছ নয়, সঠিকভাবে দায়বদ্ধও নয়।
দ্বিতীয়ত, হিন্দুত্ববাদী আক্রমন থেকে নেহরুভীয় রাষ্ট্রকে বাচানোর জন্য সেকুলারিজমকে ব্যাবহার করা হয়। এখানে সেকুলারিজম বলতে সরকারি ও ধর্মীর প্রতিষ্ঠানের কোন পৃথকীকরণ বোঝানো হচ্ছেনা, বরং ইন্ডিক বিশ্বাস ধারা (হিন্দুবাদ, জৈনবাদ, শিখবাদ) এবং অ-ইন্ডিক বিশ্বাস ধারার (খৃষ্টবাদ, কিন্তু প্রধানত ইসলাম) মাঝে একটি ক্রমধারা স্থাপন করা বোঝায়। সেকুলারিজমকে এখানে মৌলিক পশ্চিম মূল্যবোধের সাথে ভারতের সামঞ্জস্যশীলতার চিহ্ন হিসেবে দেখা হয় যেখানে এটি পশ্চিম ধনিকতন্ত্রগুলোর মতো করে একটি সহিষ্ণু সমাজ উপস্থাপন করে।
তৃতীয়ত, সেকুলারিজম ভারতের নাগরিক শান্তি বজায় রাখার একটি জরুরী অস্ত্র হিসেবে দেখা হয়, বিশেষ করে হিন্দু সংলখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলিম সংখ্যালঘুদের মধ্যকার উত্তেজনা মেটানোর জন্য। ভারতের সেকুলাজিম তাই একটি সংখ্যালঘু মুসলিম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিরাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখাশোনা করে। ভারতীয় সেকুলারিজমের আরো অনেক শাখা আলাপ থাকলেও, মুসলিম জনগনকে দেখাশোনা করার ব্যাপারটা এর প্রধানতম চিন্তা।
ভারতীয় সেকুলারিজম তবে (ভারতীয় গণতন্ত্রের মতোই) একটি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রাতিষ্ঠানিক কাটামোর সাথে একসাথ হয়ে থাকে যেখানে প্রধানতম শিকার হচ্ছে মুসলিমরা (ব্র্যাস, ২০০৩)। সেকুলারিজম এই হিন্দু-মুসলিম সংঘাতকে সমকালীন ভারতের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য আকারে না দেখিয়ে একটি ব্যাতিক্রম হিসেবে দেখাতে চায়। হিন্দু-মুসলিম সহিংসতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দাঙ্গা ব্যাবস্থা যার মাধ্যমে এগুলো সম্পাদিত হয়ে থাকে এগুলো একটু যত্নের সাথে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারতীয় সেকুলারিজম সহিংসতা কমায়নি বৈ এটাকে আরো অদৃশ্যমান করে দিতে চেয়েছে (ব্র্যাস: ৩৭৭-৮০)। বরঞ্চ এই উপসংহারে আসা যায় যে, ভারতের সেকুলারিজম এবং ‘পরিকল্পিত দাঙ্গা’ একটি প্রাতিষ্ঠানিক গঠনের অংশ যা ভারতে অবস্থানরত মুসলিমদেরকে শৃঙ্খলীকরণ ও গৃহপালিকরনের প্রকল্প পরিচালনা করে। এই শৃঙ্খলীকরণ প্রকল্প ভারতীয় গণতন্ত্রের গুণগানের সাথে মিলে ভারতে অবস্থানরত মুসলিমদেরকে জিহাদি প্রভাবমুক্ত হিসেবে উপস্থাপন করে। এই উপস্থাপনা মেনে নেয়া যাবে কেবল তখন যেখন কেউ কাশ্মিরের ঘটনাগুলো উপেক্ষা করবে যেখানে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কাশ্মীরি মুসলিমদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অনেক বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিকঃবেসামরিক উপস্থিতি-অনুপাত বজায় রেখেছে। সেকুলারিজমের জরুরত বোঝানোর জন্য ভারতীয় এবং পশ্চিম উভয় বয়ানেই ভারতের জাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে এর সংখ্যালঘু মুসলিমদের সম্পর্কের উপর আলোচনা ঘিরে ধরা হয়।
সংলাপের সম্ভাবনা এবং নাগরিক শান্তি বজায়ের সাথে সেকুলারিজমকে গুলিয়ে ফেলার পেছনে একটি অন্তর্নিহিত ধারণা কাজ করে যে, ধর্ম হচ্ছে বিপজ্জনক কারণ এটি যে ধরণের সহিংসতার জন্ম দেয়ার সক্ষমতা রাখে তা অদ্বিতীয়। অতএব, সেকুলারিজম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক ধরণের অবস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কেন ধর্মীয় প্রেরণা অন্য যেকোন প্রেরণা হতে বেশি সহিংস? এর উত্তর দেয়া হয় যে, কেউ যদি মনে করে সে ‘খোদায়ী দায়িত্ব’ হাতে নিয়ে আগাচ্ছে তারা পার্থিব কোন দিক থেকে কোন আপত্তি আসলে সেটাকে আমলে নিবেনা, এবং তারা ‘আদর্শ পারস্পারিক যোগাযোগের’ কথোপকথনে অংশ নেয়ার মতো হিসেবে নিজেদের ভাববেনা। এই উত্তর মূলত ধর্ম নিয়ে না, বরং একটি উচ্চতর কর্তা একজনের অবস্থানকে সংজ্ঞায়িত করছে তা নিয়ে। এই উচ্চতর কর্তা খোদা বা বহু খোদার রূপ নিতেই হবে এমন কোন কথা নেই, এটি হতে পারে, ইতিহাস, বিজ্ঞান কিংবা যুক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বলা যায় যে সেকুলারিজম কিছু গোত্রের উচ্চতর কর্তা গোপন করে অন্য কিছু গোত্রের বিরুদ্ধে, এবং এটি তা করে একটি উপনিবেশী নাটকের আলোকে যেখানে পশ্চিমের বিজ্ঞান আছে, আর অ-পশ্চিমের আছে কুসংস্কার।
- পশ্চিমা প্রকল্প তার ৫০০ বছরের ইতিহাসে এমন একটি ভাষা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যা সমগ্র বিশ্বকে তার পুর্ণ মাত্রায় বুঝতে সাহায্য করবে। বুঝা-ধরার এই পদ্ধতি একেক সময়ে একেক নাম নেয়: কখনো ‘যুক্তি’, কখনো ‘ইতিহাস’, কখনো ‘বিজ্ঞান’ – আমি একে ওয়েস্টার্নিজ বলে ডাকি। (পৃ. ১৯)